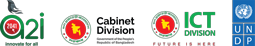-
-
About District
About District
History-Tradition
Miscellaneous
- আমাদের সম্পর্কে
-
আমাদের সেবা
প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ
-
Government office
Education and culture
Law and order and security matters
Information and Communication Technology
Agriculture and Food Affairs
-
অন্যান্য কার্যালয়
বিভাগীয়/ উপজেলা কার্যালয়
- ই-সেবা
-
Local Gov
City Corporation
Zilla Parishad
Upazila Parishad
Union Parishad
- গ্যালারি
-
যোগাযোগ
যোগাযোগ ম্যাপ
-
মতামত
-
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
- Rejulation
-
-
About District
About District
History-Tradition
Geographic & Economic
Miscellaneous
- আমাদের সম্পর্কে
-
আমাদের সেবা
প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ
-
Government office
Education and culture
Law and order and security matters
Information and Communication Technology
Agriculture and Food Affairs
-
অন্যান্য কার্যালয়
বিভাগীয়/ উপজেলা কার্যালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর
- ই-সেবা
-
Local Gov
City Corporation
Zilla Parishad
Upazila Parishad
Union Parishad
-
গ্যালারি
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
Audio
-
যোগাযোগ
অফিস যোগাযোগ
যোগাযোগ ম্যাপ
-
মতামত
-
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
-
Rejulation
Regulation of Head office
Rejulation of District office
ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। এর ভূখণ্ড ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (বিবিএস ২০২০ অনুসারে)[১] অথবা ১,৪৮,৪৬০ বর্গকিলোমিটার (সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক ২০২১ অনুসারে)[২] এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব জুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তবে পূর্বে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের স্থল সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কিলোমিটার যার ৯৪ শতাংশ (৯৪%) ভারতের সাথে এবং বাকী ৬ শতাংশ মিয়ানমারের সাথে। বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য' ৫৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট সীমানা দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কিলোমিটার বা (২৯২৮ মাইল)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতগুলোর অন্যতম।
বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি থেকে উৎপাদনমুখী শিল্পে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি। বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় একটি অংশ হচ্ছে রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাক শিল্প।
বাংলাদেশ একটি নিম্ন-মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল বাজার অর্থনীতি।[৩৯] এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে মধ্যমহারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, আয় বণ্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানী, খাদ্যশস্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমহ্রাসমান নির্ভরতা এবং কৃষি খাতের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে অন্যতম।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজাত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এসময় পাট রপ্তানি করে দেশটি অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করত। কিন্তু পলিপ্রোপিলিন পণ্যের আগমনের ফলে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই পাটজাত দ্রব্যের জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্য কমতে থাকে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]
বাংলাদেশের মাথাপিছু স্থূল দেশজ উৎপাদন[৪০] স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭০-এর দশকে সর্বোচ্চ ৫৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে এ প্রবৃদ্ধি বেশিদিন টেকেনি। ১৯৮০-এর দশকে এ হার ছিলো ২৯% এবং ১৯৯০-এর দশকে ছিলো ২৪%।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]
বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে ৩৫ তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে (পিপিপি) ২৯ তম যা দক্ষিণ এশিয়ায় ২য়। বাংলাদেশ গত এক দশক ধরে গড়ে ৬.৩ শতাংশ হার ধরে রেখে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং বর্তমানে বিশ্বের ৭ম দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি। ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুসারে (পিপিপি) বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ৪,৬০০ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ২০১৯ সালের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৭,০০,০৯,৩৫৩ জন।[৪১][৪২][৪৩]
২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ৩১৭.৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২০ সালে অনুমিত ৮৬০.৯১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৪][৪৫]
২০১৮, ২০১৯ সালে জিডিপির হার ছিল যথাক্রমে ৮ % এবং ৭.৯ %। ২০২০, ২০২১ সালে সম্ভাব্য হার হবে যথাক্রমে ২ % ও ৯.৫ %।[৪৫]
ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান
[সম্পাদনা]
একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক খাতের অবদানের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও ১৯৯০ এর দশকে অর্থনীতি ব্যাপকভাবে উন্নতি লাভ করেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিদেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও ভুগছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ এর অদক্ষতার মতো বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় বাধা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত বর্ধমান শ্রমশক্তি যা কৃষিক্ষেত্র, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, এবং ধীর প্রয়োগ অর্থনৈতিক সংস্কার, বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আবহাওয়ার উন্নতি এবং মূলধন বাজার এর উদারকরণের কিছুটা অগ্রগতি করেছে, উদাহরণস্বরূপ, এটি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা করেছে, রান্নার গ্যাসের দেশব্যাপী বিতরণকে আরও ভাল করেছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর নির্মাণ শুরু করেছে। আমলাতন্ত্র, পাবলিক সেক্টর ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্বার্থান্বেষী স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির বিরোধিতার কারণে অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রগতি থমকে আছে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS